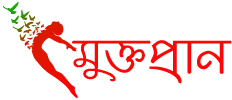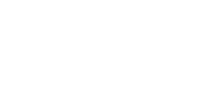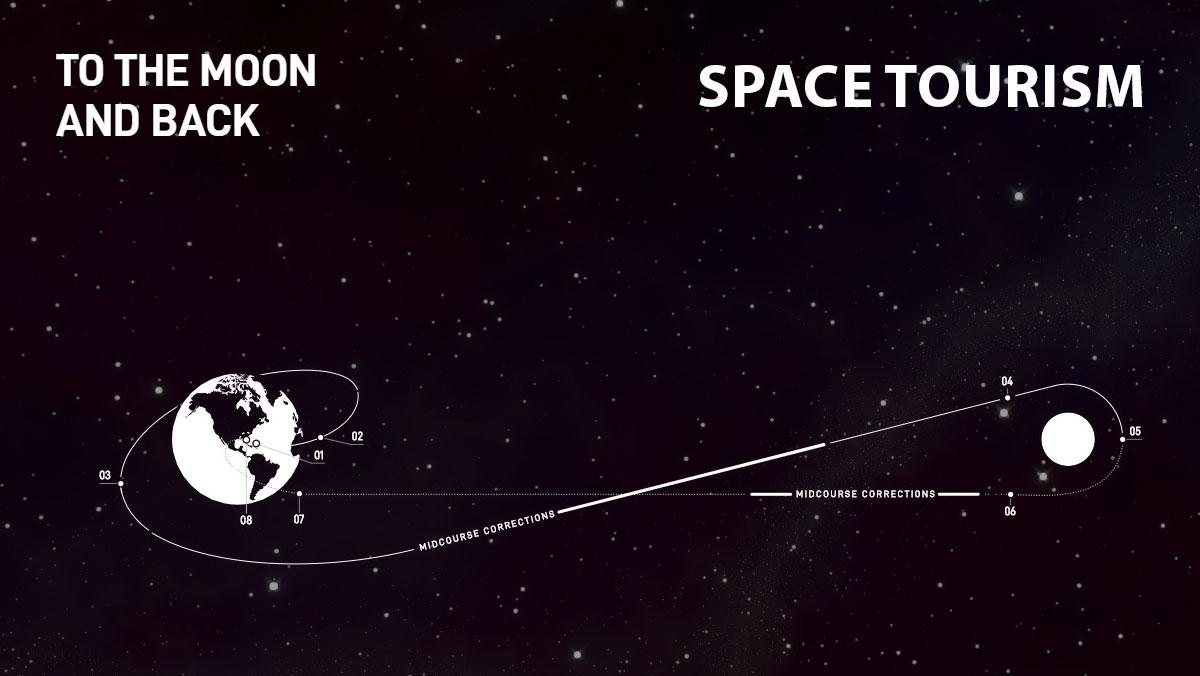প্রাচীন যুগে মানুষ সাধারণত প্রকৃতি থেকে আহরিত ফলমূল, এবং শিকার করা পশু খেয়ে জীবন নির্বাহ করতো,সমুদ্র অথবা নদীর ধারে হলে মাছ এবং জলজ প্রানীও খেত। বড় পশুদের সাধারণত অন্য হিংস্র মাংসাশী পশুরা শিকার করতো এবং তাদের ফেলে যাওয়া হাড়গোড় ইত্যাদি পাথর দিয়ে ফাটিয়ে তার ভিতরকার অস্থিমজ্জাগুলো খেত। সমাজের এই অবস্থাটাকে আমরা Hunter-gatherer স্টেজ বলে জানি।
বিভিন্ন প্রকার Archaelogical exploration এর তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি, পাথরের অস্ত্রের উন্নতির সাথে সাথে বড় বড় পশুদেরকে নিজেরাই শিকার করা ধরলো। এই বড় বড় প্রানীদেরকে শিকার করার জন্য একজাতীয় সমঝোতা এবং সহযোগিতার প্রয়োজন হত এবং ছোটবড়, আহত-দুর্বল সবাই একধরনের ভাগ পেত।
খাবার সংরক্ষনের কিছু ব্যবস্থা ছিল যেমন বরফের তলায় রাখা অথবা মরু অঞ্চলে শুকিয়ে রাখা তবে খাদ্যদ্রব্য অল্প দুয়েকদিনের ভেতরেই খেয়ে ফেলা হোত।ক্লো্নে ক্লোনে সংঘর্ষ ও হতো এবং কোথাও কোথাও মানুষ খেয়ে ফেলা বা Cannibalism এর প্রাকটিস ছিল। সমাজের এই অবস্থাটাকে কেউ কেউ আদিম সাম্যবাদী সমাজ বলে বর্ননা করেছেন। কিছুদিনের ভিতর আগুনের আবিষ্কার হয় এবং মানুষ মাংস ঝলশিয়ে খাওয়া শুরু করল। এই সময় মানুষের গায়ে তেমন চর্বি ছিলনা, এবং বন্যপ্রানীর হাত থেকে রেহাই পেতে, এবং শিকার করার জন্য যে দৌড়ঝাপ করতে হত তাতে শরীরে চর্বি জমতে পারতও না।
বিভিন্ন প্রকার Fossil থেকে, গুহার ভিতর থেকে আবিষ্কার হওয়া অস্থি থেকে, এগুলোর এক্স-রে এবং ডি এন এ বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। এইসব পরীক্ষা থেকে সেই সময়ের রোগ-বালাই সম্বন্ধেও কিছু আইডিয়া আমরা পেয়ে থাকি।
পাথরের যুগের রোগ-বালাইঃ
এই সময়কালকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে,
১) পালেওলিথিক পিরিওড (২ .৬মিলিয়নবর্ষ-১০,০০০বর্ষ)
২) মেসোলিথিক পিরিয়ড (১০,০০০- ৭,০০০ বর্ষ ) এবং
৩) নিওলিথিক পিরিয়ড (৭,০০০- ৩,২০০ বর্ষ )
নিওলিথিক পিরিওড থেকে কৃষির শুরু হয় এবং নতুন ধরনের রোগ বালাই আসতে শুরু করে। পাথরের যুগের সময়কালের বিভিন্ন অস্থির ফ্রাকচার, Osteoarthritis ইত্যাদি দিকনির্দেশ করে গাছ থেকে পড়ে যাওয়া, মারামারি, বিভিন্ন ধরনের আঘাত অথবা অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য Fatigue fracture হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। ঐ সময়ে ইনফেকশনের পক্ষে কিছু প্রমান পাওয়া যায় যা পরবর্তীকালে কৃষির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাথরের যুগে মেটাবলিক সিন্ড্রমের মত কোন রোগ পাওয়া যায় নাই, কারন তখন খাদ্য সংগ্রহের জন্য দৌড়াতে হত। তখন খাবারে প্রোটিনের পরিমান বেশী ছিল, ফল থেকে ভিটামিন, মাংশ থেকে প্রোটিন ছাড়াও ফ্যাট এবং অল্প কিছু কারবোহাইড্রেট পাওয়া যেত। মানুষ সহজেই প্রোটিন হজম করতে পারতো, চর্বিও সহজপাচ্য ছিল, ফল থেকে মিনারেলস পাওয়া যেত, মানুষ লড়াই করার জন্য উপযুক্ত ছিল।
মানুষের হাতের গঠন (Apposable Thumb) যা দিয়ে সুক্ষ কাজ করা যায়, ব্রেনের সামনের দিকের অংশ (Frontal lobe) তাকে আলাদা করেছে অন্যান্য প্রানি থেকে-এর ফলে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ক্রমশ মৌখিক ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার তাকে আরও পারদর্শী করে তুলেছে। এই সময়ে মানুষ স্থায়ীভাবে কোথাও বাস করত না। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তারা মাইগ্রেট করতো।
কৃষি যুগে রোগ বালাইঃ
১) নিওলিথিক যুগ থেকেই কৃষি কাজ শুরু হয়। যব, ভুট্টার চাষ শুরু হয় কোন কোন স্থানে, সাথে সাথে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থারও প্রয়োজন তৈরি হয়। এই সময়টাতে মানুষ আপতকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য খাদ্য মজুদ করে রাখতে শিখলো। এইসময় তারা ম্যালেরিয়া, টিউবারকুলোসিস এই দুই রোগে বিশেষভাবে ভুগতো। তাছাড়া বিভিন্ন রকমের দাঁতের রোগ যেমন ডেন্টাল কেরিজ, ক্যাভিটি ইত্যাদি খুবই কমন ছিল।
কৃষির সাথে এসেছে দুটি উপাদান। বিভিন্ন প্রানী, এবং উদ্ভিদকে গৃহপালিত (Domestication) করন, এর ফলে আমরা গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল, পাখী যেমন পেয়েছি, তার সাথে যোগ হয়েছে বিভিন্ন Zoonotic disease, Reverse Zoonotic disease ইত্যাদি। প্রানী থেকে আসা এসব রোগ ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের ভিতর, আবার মানুষ থেকেও নতুন রোগ ছড়িয়ে পড়েছে প্রানীর ভিতর
২। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও একই কথা। এখানে মানুষ স্থির হতে শিখেছে, বানিয়েছে শহর, নগর, নিজেদের জমি, বিত্ত-বৈভব। মানুষের ভিতর শ্রেনীভেদ সৃষ্টি হয়েছে, দখলদারিত্ব নিয়ে সংঘাত তৈরি হয়েছে, বনজঙ্গল সব উধাও হয়ে যাচ্ছে। একস্থান থেকে অন্যস্থানে পন্যের আদান-প্রদান বেড়ে গেছে, বানিজ্য, আমদানী-রফতানি সবই বেড়েছে। চারিদিকে শুধু উন্নয়ন, খাওয়ার মুখ অনেক, সুতরাং সবুজ বিপ্লব করতেই হবে।
একটা স্পেসিস ধংস্ব করে ফেলছে অন্য স্পেসিসগুলোকে, প্রয়োজনে কোনটার বংশবৃদ্ধিও করাচ্ছে, সবই মানুষের প্রয়োজনে। মানুষের ভিতর ভেদাভেদ শুরু হয়েছে, শ্রেনীবিভক্ত, ধর্ম-বিভক্ত হয়ে পড়েছে মানুষ,সমাজ ও রাষ্ট্র। এইসময় ইনফেক্সাস ডিজিস ছড়িয়ে পড়েছে, ইনফেকশন চেইন বজায় রাখার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছু আছে এই সমাজে।
এত মানুষ, বাকা-তেড়া, উচু-নীচু, সবল-দুর্বল, সুস্থ-অসুস্থ সব ধরনের মানুষ। সবাইকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, চিকিৎসাবিদ্যার উন্নয়ন ঘটছে, প্রাকৃতিক বিবর্তনের বদলে কৃত্রিম বিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। কেউ কেউ এখন বলে থাকেন, কৃষি বিপ্লব আসলে একটা অভিশাপ। সংক্রামক রোগগুলো সুযোগ পেলেই মহামারী, অতিমারী বা বৈশ্বিক মহামারীর রুপ নিচ্ছে। এখনকার আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতিও তাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারছে না।
কৃষিজমিতে কাজ করার জন্য লোকবলের অভাব দেখা দিয়েছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে দাস সংগ্রহ করে জমিতে কাজ করানো হচ্ছে। আফ্রিকা থেকে লোক ধরে নিয়ে গিয়ে দক্ষিন আমেরিকার জমিতে আখ চাষে ব্যবহার করা হচ্ছে, চিনির সাথে সেইসব লোকদেরকে আবার ইউরোপে পাচার করা হচ্ছে শিকল বেঁধে। পুর্ব ইউরোপ, রাশিয়া থেকে সাদা মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যে, তুরস্কে।
এইসব দাস ব্যবসার ফলে দাসরা মারা গিয়েছে ভ্রমনের অমানবিক নির্যাতনে, পুষ্টিহিনতায়, বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে। এইসব দাসদের কোন মানবাধিকার ছিলনা, তাদেরকে মারা যায়, বেচা যায়, তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও আলাদা আলাদাভাবে বেচা যায়। এইসব ব্যবস্থা সামন্ত যুগ থেকে পুঁজিবাদের শুরু এবং মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চিনির ক্ষতিকর দিক অল্পকিছুদিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লো, এবং মধ্য আমেরিকার চিনি এবং দাস রফতানি কমে গেল।
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে। ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৬ শতাংশের নীচে, সেখানে মানুষ ধার করতে হচ্ছে বিভিন্ন যুদ্ধাক্রান্ত দেশ থেকে। জাপানে বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন বাড়ার পরিবর্তে কমতে শুরু করেছে কোন কোন দেশে। দাসযুগে এবং ততপরবর্তী সামন্ত সমাজে শ্রমশোষন চলেছে অবিরতভাবে।
দরিদ্ররা তাদের প্রাপ্য পুষ্টি, লেখাপড়া এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে অনবরত। তারা এটাকে তাদের ভাগ্যের লিখন বলে মানতে শিখেছে, কারন এমনটাই তাদের মনোজগতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইসময় মেদস্ফীত জমিদার, ভুস্বামী বা রাজা রাজড়াদের ভিতর অসংক্রামক রোগ দেখা দিলেও তা ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি সাধারন মানুষের ভিতর।
কায়িক পরিশ্রম, দূর দুরান্তে যাওয়া আসার জন্য পায়ের উপর এবং গৃহপালিত জন্তুর উপর নির্ভর করার ফলে তারা অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকতেন। তবে গনোরিয়া, সিফিলিস, লিভার সিরোসিস যারা অনিয়ন্ত্রিত জীবন কাটাতেন তাদের কমবেশি সবারই হতো। মেদস্ফীত লোকেরা ভুগতে শুরু করেছিলেন বাতের ব্যাথায়( Gout) আর গরীবেরা ভুগতেন অপুষ্টি, রক্ত শুন্যতায়, এবং বিভিন্ন কৃমিজাত রোগে।
কৃষি সমাজের সঙ্গে এসেছে বিভিন্ন জীবানু নাশক, পেস্টিসাইড ইত্যাদির ব্যবহার। এই Contaminated food গুলো , আমরা খাচ্ছি এবং বিভিন্নধরনের পীড়ায় আমরা আক্রান্ত হচ্ছি। কৃত্রিম সার এবং কীটনাশক প্রয়োগ করে উৎপাদনশীলতা কয়েকগুন বৃদ্ধি করা হলেও এগুলো মাটির অম্লত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে, মাটির অভ্যন্তরের উপকারী ব্যাকটেরিয়া ধংস্ব করে ফেলছে। যদিও মানুষ এখন আবার অরগানিক চাষাবাদে মনোনিবেশ করেছে, তবুও ব্যপকভাবে এর বিস্তার নেই।
পুঁজিবাদী সমাজের রোগ- বালাইঃ
পুজিবাদী সমাজ প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত। আমাদের মত দেশ যেখানে সামন্তবাদের অবশেষ এখনও রয়ে গেছে, আর শিল্পোন্নত পুজিবাদী দেশসমূহ যেখানে পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ, আগ্রাসন, হেজিমনি ইত্যাদি রয়েছে। এরা অন্যান্য দেশকে শোষন করে সম্পদ জড়ো করছে, নিজের দেশের লোককে ভাল রাখছে, অন্যান্য দেশের লোক তাদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে বাধ্য হচ্ছে। স্থানীয় ভেষজ এবং অন্যান্য চিকিৎসা তারা হারিয়ে ফেলেছে, এ ব্যাপারে রিসার্চেও নেই মেধাবীদের অংশগ্রহন। ফার্মা কোম্পানির বহুজাতিক মার্কেটিং এ এখন আমরা সমর্পিত।
আমি আধুনিক চিকিৎসার বিরোধিতা করছি না, কিন্তু পাশাপাশি ভেষজ চিকিৎসা হয়তো আমাদের জন্য কম খরচের একটা ব্যবস্থা হতে পারতো। আমাদের মত দেশগুলিতে সংক্রামক রোগের (Communicable disease,CD) প্রভাব থেকে গেল, তারসঙ্গে বেড়ে উঠতে লাগলো ক্রমশ অসংক্রামক রোগীর (Non-communicable disease, NCD) সংখ্যা, প্রথমে শহরে তারপর গ্রামাঞ্চলে।
এখন যেখানে শহরাঞ্চলে NCD:CD প্রায় ৭০-৭৫ঃ২৫-৩০, সেখানে গ্রামাঞ্চলে NCD:CD এর সংখ্যা ৪৯ঃ৫১। আমাদের গ্রামীন অর্থনীতির উপর পুঁজিবাদ হানা দিয়েছে, Consumarism হানা দিয়েছে আরও ভয়ঙ্করভাবে। পেশার বিভিন্নতা দেখা দিচ্ছে, ইউটিউবার, টিক্টকার, লাইকী বিশেষজ্ঞ চারিদিকে। এসবের স্বাস্থ্য প্রতিক্রিয়া অল্পদিনের ভিতরই টের পাবে গ্রামীন জনগন।
NCD গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিস্তার লাভ করেছে মেটাবলিক সিন্ড্রোম। স্থুলতা, হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, গেটেবাত, হার্ট ডিজিস,কিডনী রোগী, স্ট্রোকের রোগী এখন ঘরে ঘরে। সাথে বেড়েছে ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা। জি এম ফুড, কৃত্রিম সার, কীটনাশক ইত্যাদি প্রান- আর প্রকৃতি ধ্বংস করে চলেছে, তার সাথে যোগ হয়েছে আমাদের কংক্রিট- সিমেন্ট সংস্কৃতি, কিছুদিন পরেই ধানী জমির অভাব আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাব।
নানারকম অটো-ইমিউন ডিজিস, অকুপেশনাল ডিজিসে ভুগছে সাধারন লোকজন। ভ্যাক্সিন দিয়ে কিছু কিছু রোগ প্রতিরোধ করা গেলেও আমরা এখন MDR-TB, Novel Viral infection এর কাছে অসহায়।
সমাধানের পথঃ
শোষনহীন, বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক, প্রকৃত শিক্ষিত সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলতে হবে। প্রান-প্রকৃতির ক্ষতি করে এমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না, নিলেও সেটা বৃহত্তর জনগনের উপকারে লাগতে হবে।